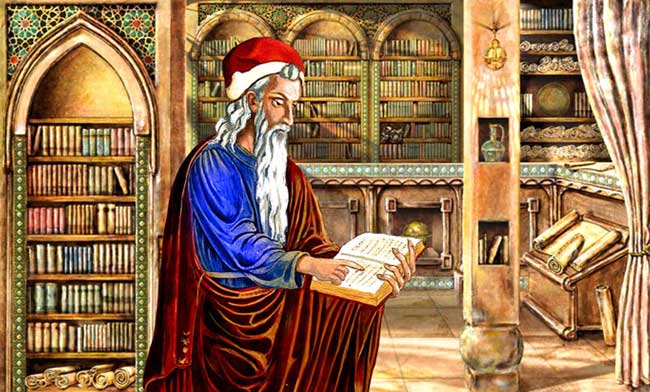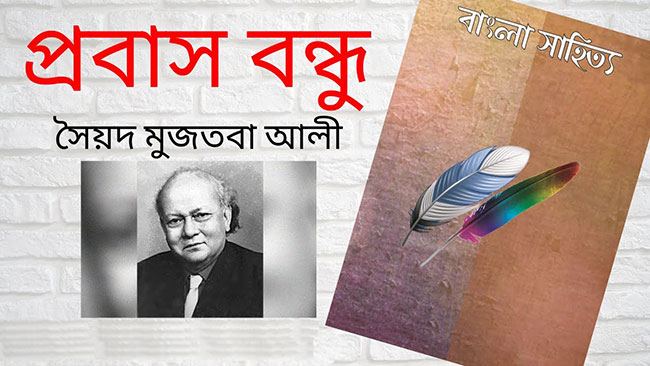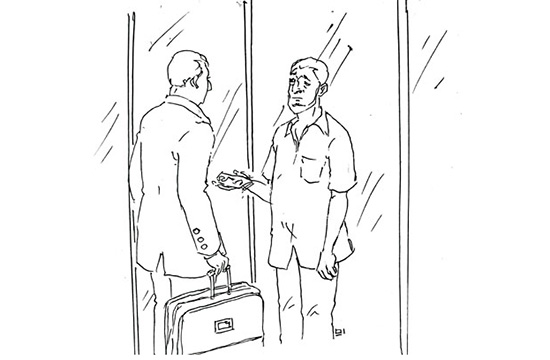তারাবি নিয়ে জসীমউদদীনের কবিতা
আধুনিক যুগে বাঙালি মুসলমান তার ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি নিয়ে কাব্য-কবিতা লেখে সেই উনিশ শতক থেকেই। কিন্তু এসবের অধিকাংশই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠেনি। অধিকাংশই ধর্মীয় বিশ্বাসের স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। বিশ্বাসের স্তর অতিক্রম করে সাহিত্যের পর্যায়ে উঠে আসার প্রথম নজির স্থাপিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের হাতে। ঈদের কথাই ধরা যাক। ঈদ দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্মীয় পবিত্রতার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের কলমে চিত্রিত হয়ে আসছিল। সেসবের মধ্যে সাহিত্যরসের সমাবেশ ঘটে তখনই, যখন নজরুল এর মধ্যে একটা মানবিক উদযাপনের রং লাগিয়ে বলে ওঠেন, ‘আজিকে এজিদে হাসানে হোসেনে গলাগলি,/দোজখে ভেশতে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,/শিরি ফরহাদে জড়াজড়ি।/সাপিনীর মতো বেঁধেছে লায়লি কয়েসে গো,/বাহুর বন্ধে চোখ বুজে বঁধু আয়েশে গো!/গালে গালে চুমু গড়াগড়ি।’
নজরুলের পর জসীমউদ্দীনের হাতে বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় সংস্কৃতি আরও নিবিড়ভাবে কাব্যরূপ পেয়েছে। এমনকি নজরুলের কবিতায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেখানে বিশেষ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে জসীমউদ্দীনের কবিতায় সেখানে ওই অনুষ্ঠানাদি একটি বৃহৎ জনেগোষ্ঠীর যাপন-সংস্কৃতির অংশ হিসাবে উঠে এসেছে। ফলে ব্যাপারটা আর শুধু ধর্ম থাকেনি, মানবিক ভাষ্যও নয় শুধু। হয়ে উঠেছে ওই সময়ের বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক উদযাপনের অংশ। তার মাটির কান্না কাব্যগ্রন্থের ‘তারাবি’ সেই রকম একটি কবিতা।
কবিতাটির মধ্যে তারাবির ধর্মীয় মাহাত্ম্য-পবিত্রতার ব্যাপারটা আছে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে ওই তারাবিকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের সম্মিলিত পুঁথিপাঠ উপভোগ। পুঁথির বিষয় ধর্মীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পবিত্রতাকে চাপিয়ে উঠেছে বাংলাদেশের এক সময়কার গ্রামের মানুষের সংস্কৃতিচর্চার বিশেষ এক রূপ। কবি যখন বলেন, ‘মৈজুদ্দীন মামলায় মোরে করিয়াছে ছারখার/টুটি টিপে তারে মারিতাম পেলে পথে কভু দেখা তার।/আজকে জামাতে নির্ভয়ে সে যে বসিবে আমার পাশে,/তাহারো ভালর তরে মোনাজাত করিব যে উচ্ছ্বাসে।/মাহে রমজান আসিয়াছে বাঁকা ঈদের চাঁদের ন্যায়,/কাইজা ফেসাদ সব ভুলে যাব আজি তার মহিমায়’, তখন এটি ধর্মীয় মাহাত্ম্যরে প্রতি আনত হয় সত্য। কিন্তু ‘এহোঃ বাহ্য’।
আসল ব্যাপার গ্রামে একটা সাজসাজ রব পড়ে যায় তারাবিকে কেন্দ্র করে। কারণ, এ তারাবির রাতে গ্রামে মোল্লাবাড়িতে জমে উঠবে পুঁথি পড়ার উৎসব। উৎসবই যদি না হবে তো কবি কেন এভাবে ঘোষণা দেবেন, ‘তারাবি-নামাজ পড়িতে যাইব মোল্লাবাড়িতে আজ,/মেনাজদ্দীন কলিমদ্দীন আয় তোরা করি সাজ।/চালের বাতায় গোঁজা ছিল সেই পুরাতন জুতা জোড়া,/ধুলা বালু আর রোদ লেগে তাহা হইয়াছে পাঁচ মোড়া;/তাহারি মধ্যে অবাধ্য এই চরণ দু’খানি ঠেলে,/চল দেখি ভাই খলিলদ্দীন লণ্ঠন-বাতি জ্বেলে!/ঢৈলারে ডাক, লস্কর কোথা, কিনুরে খবর দাও,/মোল্লাবাড়িতে একত্র হব মিলি আজ সারা গাঁও।’ এরপরই কবি আসল কথাটি পাড়লেন। বললেন, ‘ভুমুরদি কোথা, কাছা ছাল্লাম আম্বিয়া পুঁথি খুলে,/মোর রসুলের কাহিনি তাহার কণ্ঠে উঠুক দুলে।/মেরহাজে সেই চলেছেন নবী, জমজমে করি স্নান,/অঙ্গে পরেছে জোছনা নিছনি আদমের পিরহান।/’ শুধু মেরাজে যাবার কাহিনি নয়! ‘বচন মোল্লা কোথায় আজিকে সরু সুরে পুঁথি পড়ি,/মোর রসুলের ওফাত কাহিনি দিক সে বয়ান করি।’ এই কথা বলেই কবি নবিজির ওফাতের কাহিনিতে ঢুকে পড়েছেন কবিতার মধ্যে। শুধু তাই নয়। এ কাহিনি সম্মিলিত শ্রোতাদের মধ্যে কেমন ভাবাবেশ তৈরি করে তারও বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন। ফলে কবিতাটি এক সময়ের বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের যাপন-সংস্কৃতির এক বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে। এ যাপন-সংস্কৃতি হয়তো শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজে খুব একটা হালে পানি পাবে না। এটা হয়ত কিছুটা গ্রাম্যতার বর্গে চিহ্নিতও হয়ে উঠতে পারে!
কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ ধরনের সাহিত্য তখনই কেবল রচনা করা যায় যখন নিজের সংস্কৃতি নিয়ে কোনো হীনম্মন্যতা কাজ করে না। একইসঙ্গে সম্প্রদায়গত এ ধরনের সাহিত্য রচনার জন্য একটি প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক মন থাকতে হয়; আত্মবিশ্বাসী মন। জসীমউদ্দীনের মধ্যে এর সবই ছিল।
আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি নিয়ে হীনম্মন্যতা ছিল বরাবরই। শুধু নিজেরটা নিয়ে না। হিন্দুরটাও নিয়ে। এজন্য সে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত হিন্দু মনে করে না। মনে করে ধর্মহীন; ‘মানুষধর্মের’। নিদেন পক্ষে ব্রাহ্ম না হয়ে যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে খুব স্পষ্ট করে বলছেন, আমি হিন্দু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী চমকে ওঠার মতো একটি মন্তব্য করেছিলেন তার ‘বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্ম্’ প্রবন্ধে। কথাটা এ রকম, ‘তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত, পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত।’ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যে এটা কম লক্ষ করা যায়। এটা হীনম্মন্যতা বটে! জসীমউদ্দীনের মধ্যে এ হীনম্মন্যতা ছিল না। তিনি চিরকাল তথাকথিত বড় ও শিক্ষিত শ্রেণির বিরুদ্ধে গিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন। শিক্ষা ও আধুনিকতার গর্বে স্ফীত বাঙালি মুসলমানের তথাকথিত আধুনিকতার গালে চপেটাঘাত দিতে দিতে তিনি সাহিত্য করেছেন আজীবন। ‘তারাবি’ কবিতাটি এদিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।
সবার সাহিত্য ইতিহাসের উপাদান হয় না। জসীমউদ্দীনেরটা হয়েছে। ‘তারাবি’ তার বড় প্রমাণ। এক সময়ের ধর্মীয় সংস্কৃতির যে-নিবিড় চিত্র এতে আঁকা আছে তা এখনই ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠার উপকক্রম হয়েছে। এদিক থেকেও ‘তারাবি’ কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ। তো পড়া যাক জসীমউদ্দীনের মাটির কান্না কাব্যগ্রন্থের কবিতা ‘তারাবি’।
জসীমউদদীন